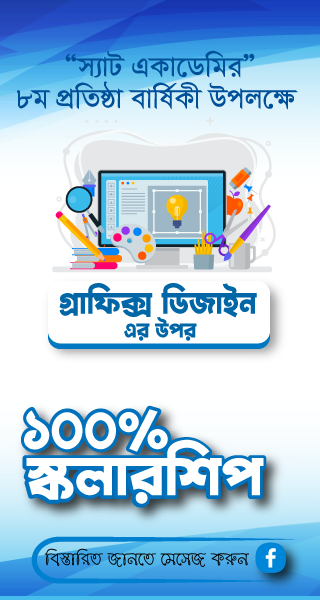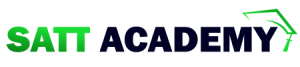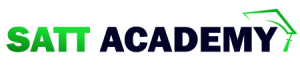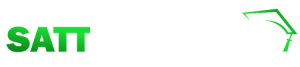ক্যারিয়ার গঠন: গুণ ও দক্ষতা
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে নবম-দশম শ্রেণিতে লেখাপড়া করার সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমরা ইতোমধ্যে জীবনে কে কোন ধরনের ক্যারিয়ার গড়ব সে বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরই আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কীভাবে সুগঠিত করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছি। ক্যারিয়ার গঠনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন জরুরি, তেমনি নিজের মধ্যে কিছু গুণ ও দক্ষতার সন্নিবেশ ঘটানোও জরুরি। এগুলো আমরা পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করতে পারি । এ অধ্যায়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভৃতি বিষয়ে জানব। তাছাড়া নেতৃত্ব, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, সহমর্মিতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও চাপ মোকাবিলা, সময় ব্যবস্থাপনা, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ক্যারিয়ার গঠনের প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।
ক্যারিয়ার গঠনে গুণ ও দক্ষতা
ভবিষ্যতে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রথমেই নিজ নিজ ক্যারিয়ার গঠনে যত্নবান হতে হবে। ভালোভাবে ক্যারিয়ার গঠন করতে হলে বিশেষ কিছু গুণ ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু গুণ ও দক্ষতা নিচে আলোচনা করা হলো:
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
মানবজীবনে সাফল্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশেষ অথচ অদৃশ্য উপাদান । জন্মের পর থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠার সময়ে মানুষের মধ্যে অজান্তেই আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে থাকে । পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, পারিবারিক শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। মানুষ যে কোনো বিষয় বা কাজের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা নির্ভর করবে সে কেমন শিক্ষা পাচ্ছে, কেমন পরিবেশ বা সমাজে বেড়ে উঠছে এবং কোন সংস্কৃতিকে লালন করছে তার উপর। এজন্য একই বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে একেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় ।
দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হচ্ছে মনোভাব, মানসিকতা বা চিন্তার ধরন। অর্থাৎ একটি বিষয়কে কে কীভাবে দেখছে বা কীভাবে নিচ্ছে সেটিকে বলা যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি । দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষের মনোজাগতিক আদর্শ যার আলোকে সে যে কোনো বিষয়কে বিচার করে। কোনো বিষয়কে ভালোভাবে নেওয়া বা ঐ বিষয়ের প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করা কিংবা বিষয়টিকে ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে গ্রহণ করাই হচ্ছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ।
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব
পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজের সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাজের সকলের সঙ্গে আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তার স্বকীয়তা বিদ্যমান থাকে। যে যত বেশি ব্যক্তিত্ববান সে তত বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে ।
সমাজে যিনি যত জনপ্রিয় তিনি মানুষের কাছে ততটাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করা সহজ হয় এবং এ ধরনের মানুষকে সবাই পছন্দ করে। ফলে সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় । এতে সাফল্যের পথ সুগম হয় ।
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গঠন
বিভিন্নভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও শক্তিকে জাগ্রত ও প্রস্ফুটিত করে। শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মানুষ তার মনন ও চিন্তন দক্ষতাকে শাণিত করতে পারে। এর মাধ্যমে তার চিন্তা করার ধরন ও মনোভাবের পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। ফলে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব তৈরি হয় ।
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও লালন করে । এভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবের সাথে সাথে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যও পরিলক্ষিত হয় ।মানুষের মানসপট গঠিত হয় তার পরিবার ও সমাজ থেকে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যগণ কোন বিষয়কে কীভাবে বিবেচনা করেন সেটি দেখে পরিবারের অন্য সদস্যরা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। অপরদিকে সমাজে বসবাস করার পাশাপাশি মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ থেকেও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, ধর্মীয় অনুশীলন, বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিশীলিত হয় ।
মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। নানা রকমের ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রভাব মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাস্তব জীবনে কোন ঘটনা থেকে সে কী শিক্ষা পেল এবং তার কোন ধরনের অভিজ্ঞতা হলো এর ওপর ভিত্তি করে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যে কোনো ঘটনার নেতিবাচক দিকের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে এ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায় ।
মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানুষকে জীবন চলার পথ নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে মানুষের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠিত হয় । প্রত্যেক সভ্যতা ও সমাজের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও সংস্কার আছে । এসব কৃষ্টি, সংস্কার ও রীতি-নীতি মানুষের মানসিকতাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ফলে তার মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় ।
ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা
ব্যক্তিগত জীবনে বা পেশাগত কারণে মানুষকে নানা ধরনের মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হয় । ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা অনেক সহজ হয়। সম্পর্ক ভালো থাকলে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায় যা ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক।
ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক সময় কাউকে কাউকে বেশ চিন্তিত দেখা যায়, যা তার মানসিক অবস্থার উপর অনেক চাপ তৈরি করে । ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে মনের উপর থেকে অনেক চাপ কমে যায় ।
ফলে মনোযোগ ও দক্ষতার সাথে যেকোনো কাজ সম্পাদন করা যায়।
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে কাজে উৎসাহ ও মনোযোগ বাড়ে। যারা এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে তারা কোনো কাজকে হীন মনে করে না এবং কাজ করার প্রতি তাদের কোনো অবহেলা থাকে না। ফলে তারা ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে পারে।
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে যেকোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। অনেকে আছে যারা নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সমস্যা সমাধানের পথে না গিয়ে সেটিকে আরো জটিল করে তোলে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা সমস্যা সমাধান করতে চায় তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সমস্যাটির সমাধান এবং সহজেই তারা তা করতে পারে।
আত্মসচেতনতা
আত্মসচেতনতা বলতে বোঝায় নিজের ব্যাপারে সচেতনতা। অর্থাৎ নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা । কোন কাজে মঙ্গল আর কোন কাজে অমঙ্গল সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা । আমি কী কাজ করছি, কেন করছি, কোন উপায়ে করছি, কাজের ফলাফল কী, কাজটির কোনো নেতিবাচক দিক আছে কি না, কাজটির ফলে নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না? এসব বিষয়ে নিজের উপলব্ধিকে আত্মসচেতনতা বলে ।আত্মসচেতন হওয়ার গুরুত্ব
আত্মসচেতন মানুষ জীবনে কখনো বড় ধরনের বিপদে পড়ে না। কারণ তারা নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবহিত থাকে। সমাজের অন্যদের চেয়ে এ ধরনের মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে। আত্মসচেতন থাকার গুরুত্ব অনেক। আত্মসচেতন মানুষ পূর্বেই যেকোনো অমঙ্গল, বিপদ, ক্ষতি বা অনভিপ্রেত অবস্থা সম্পর্কে জানতে বা অনুমান করতে পারে। ফলে তারা পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায় । তারা বিপদে পড়লে দ্রুত সামলে নিতে পারে।
আত্মসচেতন হওয়ার উপায়
আত্মসচেতন হওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ে ধারণা রাখা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়, ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী সচেতন হয়ে যেকোনো কাজ সাফল্যের সাথে করতে পারে ।
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্ভব। নিজের অভিজ্ঞতা, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। আত্মসচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিষয়াবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান ঘটনাপ্রবাহে নজর রাখা এবং বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে
আত্মসচেতনতাবোধ তৈরি হয়। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা আত্মসচেতন হওয়ার আরেকটি দিক । যে ব্যক্তি তার পরিবেশ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানে এবং সচেতন থাকে সে নিজের সম্পর্কেও সচেতন থাকে।
ক্যারিয়ার গঠনে আত্মসচেতনতার ভূমিকা
সচেতন থাকলে জীবনের যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। আত্মসচেতন মানুষ নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরা অনুধাবন করতে পারে বিধায় ক্যারিয়ারের কোন সময়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটি ভালো হবে তা তারা বুঝতে পারে।
অনেক সময় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। গৃহীত সিদ্ধান্তটি সঠিক নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সচেতন ব্যক্তিরা সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে দ্রুত অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা তাদের ক্যারিয়ারকে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেয় ।
একজন মানুষ কতটুকু সফল তা বোঝা যায় তার অর্জন থেকে। আত্মসচেতন মানুষেরা তাদের নিজেদের অর্জন নিজেরাই মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে যায় ।
অন্যের উপর নির্ভরশীল হলে ক্যারিয়ারে সফল হওয়া যায় না। তাছাড়া অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা মানুষকে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং তারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। আত্মসচেতনতা অন্যের প্রতি নির্ভরশীল না হওয়ার শিক্ষা দেয়। আত্মসচেতন ব্যক্তিরা কখনো অন্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে না । আত্মবিশ্বাস
আত্মবিশ্বাস অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়। অর্থাৎ নিজের শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস । যেকোনো কাজ আমি যথাযথভাবে করতে পারব এবং সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হব এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে লালন ও ধারণ করাকে আত্মবিশ্বাস বলে ।আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব
আত্মবিশ্বাস যেকোনো ব্যক্তিকে সবসময় দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাসীরা নিজেদের শক্তিমত্তা ও সক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হয় বলে তারা দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পারে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ সকলের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। অন্যরা যখন দেখে কেউ খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে কোনো কাজ সম্পাদন করছে তখন তারা ঐ ব্যক্তির প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করে। আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করলে কাজটি নিখুঁত, নির্ভুল ও কার্যকরী হয় । আত্মবিশ্বাসীরা অন্যদের সমালোচনাকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর অটল থাকে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে অন্যরা তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকার কারণে যেকোনো কাজে আত্মবিশ্বাসীরা সহজেই সফলতা অর্জন করে।
আত্মবিশ্বাস অর্জনের উপায়
শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে, পরিশীলিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আত্মোপলব্ধির সুযোগ পায়। শিক্ষা মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে ও জানতে সহায়তা করে । ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার রসদ পায়।
আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে হবে। মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে সে কোন বিষয়ে দক্ষ ও কোন বিষয়ে নয়। যা সে ভালো বুঝে ও ভালো পারে তাই তার শক্তি ও সামর্থ্য। অর্থাৎ আমি কী করতে পারি বা কোন বিষয়ে আমার দক্ষতা বেশি সে বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। যে বিষয়ে আগ্রহ বেশি সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বা বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে । এতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ।
কোনো কাজ করতে গিয়ে ভুল হলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়। কী কী কারণে ভুল হলো তা চিহ্নিত করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে কাজ করলে আর ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হলে কোনো বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা যাবে না। এ কাজটি কঠিন বা এটা আমাকে দিয়ে হবে না এ রকম মনোভাব পোষণ করলে মনে সাহসের ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে আত্মবিশ্বাস কমে যায় । ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করলে কোনো কাজই কঠিন মনে হবে না এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ।
ক্যারিয়ার গঠনে আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা
যাদের আত্মবিশ্বাস বেশি তারা লক্ষ্য নির্ধারণে সবসময় অগ্রগামী থাকে । তারা ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবলের সাথে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে। কোনো ধরনের হীনমন্যতা ও অন্যের নেতিবাচক মন্তব্য তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অনেকে অল্প সময়ে লক্ষ্য অর্জনের স্বপ্ন দেখে থাকে। কোনো কারণে লক্ষ্য পূরণে দেরি হলে তারা থমকে যায়, হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু যারা আত্মবিশ্বাসী তারা দমবার পাত্র নয়। তারা জানে, একদিন না একদিন সফলতা আসবেই, তাই তারা সর্বদা লক্ষ্যমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। আত্মবিশ্বাসীরা সবসময় সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা দৃপ্ত সাহসে বলীয়ান হয়ে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কখনো তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা ঐ কাজের সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়। আমি এ কাজ পারবো কিনা বা আমার দ্বারা হবে না কিংবা এ কাজ করলে কে কী বলবে এ ধরনের ভাবনাকে হীনমন্যতা বলে। আত্মবিশ্বাসীরা হীনমন্যতাকে সহজে জয় করতে পারে।সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম উপাদান। অনেকে আছে যারা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভীত হয়ে পড়ে বা বিভিন্ন পিছুটান তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। আত্মবিশ্বাসীরা সহজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তাই বাস্তবায়ন করে থাকে।দৃঢ় প্রত্যয়
জীবনে লক্ষ্য অর্জনে চাই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন কিংবা স্বপ্নপূরণ হয় না। এ কঠিন প্রতিজ্ঞার অপর নাম দৃঢ় প্রত্যয় । দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে লক্ষ্য অর্জন ও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ব্যাপক আগ্রহ ও সুদৃঢ় মনোবলসহ কোনো কাজ করাই দৃঢ় প্রত্যয়। দৃঢ় প্রত্যয়ীরা কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কাজের বাস্তবায়নে অটুট থাকে ।
দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব
প্রত্যেক মানুষের জীবনে দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব অনেক। দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে নিজের ক্যারিয়ারকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো কাজ শুরু করলে লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা থাকে। কারণ দৃঢ় প্রত্যয়ীরা কখনো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে পিছু হটে না বরং তারা যেকোনো উপায়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো কাজ শুরু করলে তা সময়মতো সম্পন্ন হয়। লক্ষ্য অভিমুখে আপ্রাণ প্রচেষ্টা থাকার ফলে কাজগুলো একটির পর একটি সম্পূর্ণ হতে থাকে ।
দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার উপায়
দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন স্বপ্ন বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য। কারণ কোনো লক্ষ্য বা স্বপ্ন না থাকলে লক্ষ্যমুখী কোনো তৎপরতা থাকে না। এ ধরনের উদ্যোগ ছাড়া দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার সুযোগ থাকে না । তবে
স্বপ্ন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে। বাস্তবের সাথে মিল নেই, জীবনের জন্য আবশ্যকীয় নয় বা বাস্তবে তা অর্জন সুদূর পরাহত এমন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হলে লক্ষ্যকেন্দ্রিক সকল তৎপরতা হবে পণ্ডশ্রম। কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের জন্য যে যে দক্ষতা আবশ্যক তা থাকতে হবে। লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকলে কাজের শুরুতেই হোঁচট খেতে হবে। কেউ যদি লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করে তবে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হলে নিজের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। কোনো লক্ষ্য স্থির করলে তা সম্পর্কে পূর্বাপর ভেবে নেওয়া জরুরি। লক্ষ্যের ভালোমন্দ সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা উচিত। লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সচেতনতা মানুষকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে ।ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভূমিকা
ব্যক্তিগত জীবনে যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তারা সবসময় তাদের স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি অবস্থান করে। ক্যারিয়ারমুখী তৎপরতার কারণে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এতে ক্যারিয়ারে সফলতা লাভ করা যায় । যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তারা তাদের ক্যারিয়ারে কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাদের জীবনে একটার পর একটা সাফল্য আসতে থাকে এবং একসময় তারা সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে। যেমন- দৃঢ় প্রত্যয় থাকার কারণে আমাদের এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজনীন এভারেস্ট জয় করেন ।
শ্রদ্ধা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক
শ্রদ্ধা একটি সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত একটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ হচ্ছে শ্রদ্ধাবোধ । কাউকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়া কিংবা মানুষের জ্ঞান, অবস্থান, মর্যাদা ও সক্ষমতাকে সমীহ করাকে শ্রদ্ধা বলে । অন্যকে এভাবে মূল্যায়ন বা সমীহ করার যে মানসিকতা, মনোভাব ও বোধ তাকে শ্রদ্ধাবোধ বলে । যারা সমাজের অন্যদের সম্মান করে না, তাদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে চায় না, সামাজিক অবস্থানকে হীন দৃষ্টিতে দেখে ফলে তারা নিজেরাও শ্রদ্ধা পায় না। নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাবোধও গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি নিজেকে শ্রদ্ধা করে না অন্যরাও তাকে শ্রদ্ধা করে না। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করে তোলে।
মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারে না। সমাজে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে বলেই সমাজের উৎপত্তি হয় । এ কারণে সমাজের প্রতিটি সদস্য নানাভাবে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। কৃষক যেমন মৎস্যজীবীর ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মৎস্যজীবী কৃষকের ওপর নির্ভরশীল । এমনিভাবে সমাজের প্রতিটি পেশার মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ পারস্পারিক নির্ভরশীলতা গড়ে উঠে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কই আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক। বিশেষ কোনো প্রাপ্তির আশা না করে একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে যে সদ্ভাব বা সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বলে ।
ক্যারিয়ার গঠনে শ্রদ্ধা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ভূমিকা ক্যারিয়ার গঠনে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিশেষ সুফল রয়েছে। এটি লাভ করার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কর্মক্ষেত্রেও যদি শ্রদ্ধাশীলতার গুণটি ধারণ করা যায় তবে নিজে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি অন্যরাও উপকৃত হবে ।
এমন অনেক কাজ আছে যা একার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষত শ্রমবিভাজনের এই যুগে এটি আরো কঠিন । স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এর অর্থই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার গুণটি যদি কারো মধ্যে না থাকে তবে তার পক্ষে কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও এ গুণটি বিশেষ ভূমিকা রাখে । সহপাঠী বন্ধুদের মাধ্যমে অনেক সময় নতুন বিষয় বা অজানা এমন বিষয় জানা সম্ভব হয়, যা ক্যারিয়ারে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।
মানুষের জীবনে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। যাদের এ ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তারা বিপদে পড়ে কম; আর বিপদে পড়লেও দ্রুত পরিত্রাণ পায়। এদের বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় অন্যরা এগিয়ে আসে ও সহযোগিতা করে । পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা রাখে। ক্যারিয়ারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ভালো রাখার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলে সহযোগিতা পাওয়া যায় ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় ।সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা
সততা একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। সততা হচ্ছে সত্য বলা, সত্যকে ধারণ করা, সত্যকে লালন করা এবং সত্যকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জীবনের সবক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনায়, কর্মে সত্যবাদী হওয়া এবং সং মনোবৃত্তির সাথে যেকোনো কাজ সম্পাদন করাকে সততা বলা হয়। যা দেখেছি, যা করেছি, যা ঘটেছে, যা পেয়েছি কোনো কিছু না লুকিয়ে তা হুবহু উপস্থাপন করাই সততা ।
জীবন ধারণের জন্য মানুষকে কোনো না কোনো পেশার সাথে যুক্ত হতে হয় । প্রত্যেককে নিজ নিজ পেশায়
কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয় । একজন পেশাজীবীর কাছ থেকে যে কাঙ্ক্ষিত নিয়ম-নীতি ও আচরণ
প্রত্যাশা করা হয় সংশ্লিষ্ট পেশায় তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে পেশাগত নৈতিকতা। অর্থাৎ পেশায় সততা,
দায়িত্বশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে
পেশাগত নৈতিকতা।
একটি সমাজ, রাষ্ট্র, ও শাসনব্যবস্থা আইনের শাসনের উপর নির্ভর করে। যে সমাজে আইন যথাযথভাবে মানা হয় সেখানে শৃঙ্খলা থাকে। আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। আইন অনুযায়ী সব ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলা, আইনগত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ।
ক্যারিয়ার গঠনে সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব ও ভূমিকা মানবজীবনে সততার গুরুত্ব অপরিসীম। সততা মানুষকে উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতায় ভূষিত করে। সততাকে সকল ধর্মেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সততার মাধ্যমে মানুষ পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বস্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে সৎ থাকলে নিজেকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও সততা খুব গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষাজীবন থেকে সততার গুণ অর্জন না করতে পারলে ক্যারিয়ারে বেশি দূর এগোনো সম্ভব হয় না । সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সততাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে ।
বর্তমান সমাজে পেশাগত নৈতিকতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মজীবনে যিনি যে পেশায় আছেন তিনি যদি তার কাজ, সেবা ও সময়ের প্রতি সৎ থাকেন তাহলে তিনি তার পেশায় নৈতিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবেন । প্রত্যেক পেশাজীবী মানুষ যদি স্ব-স্ব পেশায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তবে তাকে কখনো পেশাগত নৈতিকতার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। শিক্ষার্থী যদি নিজে সততা, দায়িত্বশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে তবে তার ক্যারিয়ার সুগঠিত হবে এবং পেশাগত জীবনে সে নীতিবান থাকতে সক্ষম হবে।কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সবাইকেই আইন মেনে চলতে হয় এবং আইনের আওতায় থাকতে হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সবার জন্যই আবশ্যক । তেমনি কর্মজীবনেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিধিবিধান মেনে চলতে হয় । শিক্ষাজীবন থেকেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে ক্যারিয়ার গঠনে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ।
ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতাই ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় অন্যকে পরাজিত করার চেয়ে সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নিজেকে আরো উন্নত প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাই ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার, প্রতিবেশী, সহপাঠী, বন্ধু তথা সমাজের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখা হয় । যেমন- কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে চায়। এজন্য সে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, মনোযোগ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া করবে। শুধু নিজে ভালো ফল লাভ করলেই চলবে না, অন্য সহপাঠীরাও যাতে ভালো ফল অর্জন করতে পারে সে জন্য তাদের সহযোগিতা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা রক্ষা করতে হবে। ইতিবাচক প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটাতে হলে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্য কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
অন্যের সমস্যা বা বিপদে সহায়তা করার মানসিকতাই সহযোগিতার মনোভাব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক রেখে প্রয়োজনে অন্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হয়। যেমন- পারিবারিক কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করা, সহপাঠীদের ক্লাসের পড়া বুঝতে সহায়তা করা, কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তার সেবা-যত্ন করা; প্রয়োজনে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কিংবা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে সহকর্মীদের সহযোগিতা করা। পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র কিংবা সমাজ সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। কাজ করা প্রয়োজন ।
ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মনোভাবের ভূমিকা
ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত ও অন্যের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণকারীরা সহজেই সুন্দর ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে। ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণকারী হলে সহজেই অন্যের আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়। অন্যরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মূল্যায়ন করে। সে নিজে কখনো বিপদ বা সমস্যাগ্রস্ত হলে অন্যরা তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে । ফলে সহজেই পরিবার, শিক্ষাক্ষেত্র, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আস্থা ও দক্ষতার সাথে কাজ করা যায় এবং সুনামের সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ
অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেককে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়। যেকোনো দলগত কাজ বা বহুসংখ্যক লোকের একত্রে কাজ করার সময় সকলের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ পরিচালনার প্রয়োজন হয় । এক্ষেত্রে যেকোনো একজনকে ঐ দলের সমন্বয় ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের এইদায়িত্ব কোনো একজনের উপর ন্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে । সহজ ভাষায় বললে নেতৃত্ব হচ্ছে কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়া।
নেতৃত্বের ধরন :
গণতান্ত্রিক নেতৃত্বঃ এ ধরনের নেতা সব কাজে তার কর্মী বাহিনীর মতামত নিয়ে থাকেন। কর্মীরা
স্বাধীনভাবে ও চাপমুক্ত থেকে যেকোনো মতামত দিতে পারে। কর্মীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে তিনি
সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন।
ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব : এ ধরনের নেতার সবাইকে আকর্ষণ করার অপরিসীম ক্ষমতা থাকে। সাধারণত প্রবল আকর্ষণ শক্তির অধিকারী এধরনের নেতার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অন্যরা সহজে মেনে নেয়। কারণ অনুগামীরা নেতার সাথে একাত্মতা অনুভব করে থাকে । স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতা কোনো কাজেই তার কর্মী বাহিনীর মতামতকে গুরুত্ব দেন না।
তিনি তার নিজস্ব চিন্তা ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ও বাস্তবায়ন করেন ।
পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্ব এ ধরনের নেতা সমসাময়িক অবস্থা ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন । তিনি কখনো গণতান্ত্রিক আবার কখনো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন । নির্জীব নেতৃত্ব এ ধরনের নেতা সক্রিয় ও সচেতন নন। তারা কর্মী বাহিনীর সব কথা মেনে নেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেন। এরা নামেমাত্র নেতা কর্মীরা তাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না এবং কর্মীদের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না ।
নেতৃত্বের উপাদানঃ নেতৃত্ব গড়ে উঠার জন্য তিনটি উপাদান আবশ্যক। এগুলি হলো নেতা, অনুগামীবৃন্দ ও পরিস্থিতি। এই তিনটি উপাদানের সম্মিলনে নেতৃত্ব জেগে উঠেনেতৃত্বের গুণাবলি নিচে নেতৃত্বের কয়েকটি গুণ উল্লেখ করা হলো। তোমরা দলে আলোচনা করে তোমাদের মতে আর কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করো।
• যথাযথ জ্ঞান
• যোগ্যতা
• ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয়তা
• ঝুঁকিগ্রহণের মানসিকতা
• সহানুভূতি ও সহমর্মিতা
• আবেগ নিয়ন্ত্রণ অধ্যবসায়
• সময়ানুবর্তিতা
• ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যের নেতৃত্বে কাজ করার মানসিকতা
উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ
কোনো কাজ ও কাজের প্রতি আগ্রহ নিজ থেকে শুরু হয়ে যায় না। কাজের চিন্তাটি প্রথমে কোনো একজনের মাথা থেকে আসে, তারপর তিনি যখন কাজটি করার আয়োজন করেন তখনই কাজ শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াকে এককথায় বলে উদ্যোগ গ্রহণ। উদ্যোগ হচ্ছে কোনো কাজের প্রথম পদক্ষেপ। স্বাধীনভাবে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যের নির্দেশনা ব্যতিরেকে তা শুরু করে দেয়ার যোগ্যতাকে উদ্যোগ বলে। অপরদিকে কাজ করার মানসিকতাকে কাজের প্রতি আগ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ খুশিমনে আনন্দের সাথে নিজে থেকে কোনো কাজ করার ইচ্ছা বা মানসিকতাকে কাজের প্রতি আগ্রহ বলা হয়। যেমন: একজন নিজ উদ্যোগে কাজ শুরু করায় অনেকে একাজে এগিয়ে আসে।ক্যারিয়ার গঠনে নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহের ভূমিকা
পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, উদ্যোগ গ্রহণের যোগ্যতা ও কাজের প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকা প্রয়োজন । যার এসব যোগ্যতা আছে তাকে দিয়েই সবাই কাজ করাতে চায়। কর্মক্ষেত্রে যাদের নেতৃত্ব উদ্যোগ গ্রহণের যোগ্যতা ও কাজের প্রতি আগ্রহ আছে তারা সহজেই অন্যদের সমীহ আদায় করতে সক্ষম হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা দেখতে চান কর্মীর মধ্যে নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ আছে কি না। শিক্ষানবিশ কর্মীরা এ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারলে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পায়। তাই শিক্ষাজীবন থেকেই এসব দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয় ।
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার অগ্রভাগে আছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীন দেহ ও মন নিয়ে কখনোই স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। মানুষের শরীর ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে জানা ও সে অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা।
জন্মের পর থেকেই মানুষের দৈহিক বিকাশ বা শারীরিক উন্নতি ঘটতে থাকে। এ সময় সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে শারীরিক বিকাশ ভালো হয়। প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি স্বাস্থ্য বিধি জেনে সে অনুযায়ী নিজের স্বাস্থ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে। অপর দিকে দেহের সাথে মনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। মানুষের দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও সাধিত হয়। কোনো কারণে মন খারাপ হলে মানুষের কর্মক্ষমতা ও সক্ষমতা হ্রাস পায় ।
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলি
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের কাজ করতে হয়। নিচে এধরনের কিছু কাজের তালিকা প্রদান করা হলো।কথায় আছে সুস্থ দেহে সুস্থ মন। শরীর কিংবা মন যদি সুস্থ না থাকে তবে মানুষ কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। তাই যেকোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা । পারিবারিক কাজ, লেখাপড়া কিংবা কর্মক্ষেত্রের কাজ সবক্ষেত্রেই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। লেখাপড়ার সময়ে যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা যায় তবে পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায় এবং পরীক্ষায় ভালো করা যায়। ক্যারিয়ার গঠনে এ বিষয়টিরভূমিকা আরো বেশি। ক্যারিয়ারের জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ সময় শরীর ও মন ভালো না থাকলে যেকোনো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। তাই শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকর ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।
সহমর্মিতা
মানুষকে প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্রে নানা রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো তার বিপদ আসে, কখনো তার মধ্যে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় তখন মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্তবোধ করে, বিষণ্ণ থাকে কিংবা নানা দুঃখ-কষ্টে ভোগে। এমন অবস্থায় এ ধরনের মানুষের সাথে মানসিকভাবে একাত্ম হওয়াকে সহমর্মিতা বলে ।
দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত কিংবা বিপন্ন-বিষণ্ণ মানুষের বেদনা, মনোকষ্ট উপলব্ধি করে তাদের সাথে একাত্ম ও সমব্যথী হওয়াই সহমর্মিতা। অন্যভাবে বলতে গেলে সহমর্মিতা বলতে মানুষের সকল যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন ও বিষণ্নতাকে নিজের অনুভূতিতে স্থান দিয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করাকে বোঝায়। হৃদয়ের গভীরতম অংশ থেকে উৎসারিত অনুভূতিই সহমর্মিতা ।
সহমর্মিতার গুরুত্ব
মানুষের দুঃখ কষ্টে সমব্যথী হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সহমর্মিতা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে ।
পরিবারে বা সমাজের অন্য মানুষের বিপদে-আপদে সমব্যথী হলে এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করলে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন হয়। মানুষ একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং পরস্পর পরস্পরের যেকোনো ধরনের সমস্যায় এগিয়ে আসে। সমাজের সব সদস্য যদি একে অপরের সমস্যায় এগিয়ে আসে তাহলে তাদের মধ্যে আস্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। সমাজের সব সদস্য যখন একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার হবে এবং যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য
সহমর্মিতা ও সহযোগিতা আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এ দুয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য বিদ্যমান । একটি অনুভূতি সম্বন্ধীয় আর অন্যটি বাস্তব সম্পর্কিত । নিচে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো ।
ক্যারিয়ার গঠনে সহমর্মিতার প্রভাব
সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে একজন মানুষের ভেতরের মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায় । সহমর্মী ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, অন্যদের কাছে সে বিশেষ মর্যাদা পায়। এসবের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তার বিকাশ ঘটে। কারো প্রতি একবার সহমর্মিতা প্রদর্শন করলে তার সাথে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সেটি মনে রাখে। পরবর্তী সময় কর্মজীবনে বা বাস্তব জীবনে কোনো সমস্যায় পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে পূর্ব-পরিচিতির সুবাদে তার সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পাওয়ার সুযোগ থাকে ।
জেন্ডার সংবেদনশীলতা
নারী ও পুরুষ মিলেই হচ্ছে মানব জাতি। সভ্যতার শুরু থেকেই নারী-পুরুষ যার যার অবস্থান থেকে সমাজব্যবস্থার বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষের অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন হতে থাকে। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও আচরণিক ভিন্নতা দেখা দেয়। নারী-পুরুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এই সম্পর্ককে জেন্ডার বলে।
জেন্ডার মানুষের জৈবিক পরিচয়কে নির্দেশ করে না, বরং নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে । অর্থাৎ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ যা পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিকশিত হয় ।
যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমঅবস্থানে থেকে সমান কর্মদক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে
এবং সমান সামাজিক মর্যাদা ও সমান আর্থিক সুবিধাদি ভোগ করবে । এই ধারণাকে সামনে রেখে যেকোনো
কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়াকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলে ।
জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার গুরুত্ব
জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার মাধ্যমে নারী কিংবা পুরুষের বা বিশেষ লিঙ্গের প্রতি সমাজে বিদ্যমান ও
প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কমে আসবে। নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই এ ধরনের বৈষম্যের বিলোপ ঘটবে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা যদি সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে নারী পুরুষের সামাজিক ও ব্যক্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ তাদের মধ্যে এ ধারণা তৈরি করবে যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি জেন্ডার সংবেদনশীল হয় তাহলে সমাজে নারী-পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে । সমাজের কেউ কাউকে তখন হীন করার চেষ্টা করবে না এবং বিশেষ কোনো লিঙ্গের মানুষের প্রতি মানুষের বিরাগ থাকবে না। জেন্ডার সংবেদনশীলতা মানুষের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটায়। প্রত্যেকের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফলে মানুষের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমানভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। পরিবারের ক্ষেত্রেও জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন, এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হবে। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে যা পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার উপায়
নারী-পুরুষ প্রত্যেকের উচিত আগে নিজের অবস্থান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া । অন্যের অবস্থান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে বিবেচনা করলে সমলিঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধাজনক মনোভাব তৈরি হবে না। নারী-পুরুষ প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি যদি কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। পরস্পরের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ধারণা পোষণ করে জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া সম্ভব নয়। পরিবারই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । আর পরিবার থেকেই শুরু হয় প্রথম জেন্ডার বৈষম্য। তাই পরিবারকে সবার আগে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে। যদি পরিবার জেন্ডার সংবেদনশীল হয় তাহলে পরিবারের সদস্যরা জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে গড়ে উঠবে । ক্যারিয়ার গঠনে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ভূমিকা
জেন্ডার সংবেদনশীলতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রেই এর প্রভাব বেশি । কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করবে, সমান সুবিধা ভোগ করবে, এটা নিয়ম হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হলে কর্মী নিয়োগ, কর্মবণ্টন, প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত পরিবেশ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সুবিধাদি ও মর্যাদা এবং কর্মী মূল্যায়নে বিশেষ লিঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে মেধা, শ্রম ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ কিংবা কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় থাকলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি, আস্থা বৃদ্ধি পায় । এতে কর্ম পরিবেশ সুন্দর হয় । তখন সবাই নিজ নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে।
বিশ্লেষণ করা ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা
কোনো ঘটনা ঘটলে অনুসন্ধিৎসু মানুষ সে ঘটনার কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। বিভিন্ন আঙ্গিকে ঘটনা ব্যাখ্যা করে সে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই কারণ খোঁজার চেষ্টাই হচ্ছে মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতা। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কোনো ঘটনা সম্পর্কে তদন্তে গেলে তারাও এই ধরনের বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্লেষণ করার দক্ষতা মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।
সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা হচ্ছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়। এটা কখনো পূর্বনির্দেশিত নয় এবং নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে করা সম্ভব হয় না। নতুন করে কিংবা ভিন্নভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা । সৃজনশীল চিন্তন বিষয়ে 'Think out of the box' বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ । অর্থাৎ প্রথাগত কাঠামোর বাইরে চিন্তা করার দক্ষতাই হচ্ছে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা ।
বিশ্লেষণ করার ধাপ
কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এরপর বিষয় বা ঘটনার বিবরণ জানতে হবে। ঘটনার বিবরণ জানার পর ঘটনা বা বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হবে পরবর্তী ধাপে বিষয় বা ঘটনাটি বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়
সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি নেই। প্রথাগত কাঠামোর বাইরে স্বাধীন ও মুক্তভাবে চিন্তার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা, কোনো তত্ত্বকে কাগজে এঁকে, দৈনন্দিন কাজের রুটিনে পরিবর্তন এনে, কোনো সমস্যার সমাধান চিন্তা করে এবং নতুন কিছু চিন্তা করার মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় । ক্যারিয়ার গঠনে বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা
ক্যারিয়ার গঠনে বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষাজীবনে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন নানা বিষয় সামনে চলে আসে। এ সময় প্রত্যেকেই নিজস্ব বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা যদি কারো থাকে তাহলে সে সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চায় শিক্ষার্থী বা অধীনস্থ কর্মী তার নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কাজটি করুক। যারা সৃজনশীল চিন্তা করতে পারে তাদের কাছে বিষয়টি খুবই সহজ এবং তারা অনায়াসে তা করতে পারে। এজন্য যারা যত বেশি বিশ্লেষণী ও
সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী ক্যারিয়ার গঠনে তারা তত বেশি এগিয়ে থাকে ।সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা
চলার পথে মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা আবার কখনো পারিবারিক সমস্যা। আছে সামাজিক সমস্যা আবার কখনো কর্মক্ষেত্রে সমস্যা। কিন্তু তাই বলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কিংবা সমস্যাকে দমিয়ে রেখে মানুষ কাজ করে না। প্রত্যেক সমস্যারই কোনো না কোনো সমাধান আছে । গ্রহণযোগ্য একটি উপায়ে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সমস্যা সমাধান বলে ।
যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত প্রত্যেকটি কাজ শুরুই হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ যদি কোনো কাজ করব কি করব না, ভালো হবে কি হবে না এই নিয়েদ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে তাহলে ব্যক্তির সেই অবস্থাকে বলা হয় সিদ্ধান্তহীনতা । এ অবস্থা কাটিয়ে ভালো-মন্দ বিবেচনায় রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কোনো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারার ক্ষমতাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা।
সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
শুরুতেই যে সমস্যাটি সামনে এসেছে সে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সমস্যাটিকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করে করে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে। এরপর সমস্যাটি কী কারণে হয়েছে এবং কোথা থেকে এই সমস্যার উৎপত্তি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করে সমস্যাটিকে একটি সমাধানযোগ্য প্রক্রিয়ায় আনতে হবে। যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পর সেটির উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য কয়েকটি সমাধান বের করতে হবে। সমাধানগুলোর মধ্য হতে কার্যকর এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সমাধানটি গ্রহণ করতে হবে। সবশেষে গৃহীত সমাধানটি যথাযথভাবে কার্যকর কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে ।
সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
১. সমস্যা বিশ্লেষণ
২. কারণ ও উৎস অনুসন্ধান
৩. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
৪. সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণ
৫. উপযুক্ত সমাধান নিরূপণ
৬. সমাধানটি বাস্তবায়ন
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমেই তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন । সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কয়েকটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিতে হবে। বিকল্প সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই প্রথমে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে হতে হবে। বিকল্প সিদ্ধান্তসহ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং এগুলোর ফলাফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বানুমান করে নিতে হবে। নিজের বিচার ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে এটা করতে হবে। এ পর্যায়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ফলাফল ইতিবাচক হয় এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরপর গৃহীত সিদ্ধান্তটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সবশেষে গৃহীত সিদ্ধান্তটির ফলাফল মূল্যায়ন করতে হবে। যদি মনে হয় অন্য সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হতো তাহলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নতুন আরেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।ক্যারিয়ার গঠনে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার ভূমিকা
ক্যারিয়ার গঠনে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাজীবনে পছন্দের বিষয় ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর ক্যারিয়ার গঠন নির্ভর করে। আবার শিক্ষাজীবন শেষ করার পর কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের কাজে সে নিয়োজিত হবে । এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ওপর তার ক্যারিয়ার গঠিত হয়। তাই সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যথাযথ ক্যারিয়ার গঠন করা যায়।
চাপ মোকাবিলা
মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার ফলে মানসিক চাপ তৈরি হয়। দুঃখ দুর্দশা, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত কাজের ভার, শোক, যন্ত্রণা, বিপর্যয় এগুলোর ভার একা এবং দীর্ঘ সময় বহন করতে হলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক চাপ একটি মনোদৈহিক অবস্থা যা আমাদের শরীর ও মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে । কোনো কারণে দুশ্চিন্তা, মনোকষ্ট, উদ্বেগ দীর্ঘ সময় ধরে চললে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটায় । মানুষ বিচলিত হয় এবং এক পর্যায়ে ভেঙ্গে পড়ে ও ভুল পথে পা বাড়ায়। তাই চাপকে প্রশ্রয় না দিয়ে চাপ মোকাবিলা করে সামনে এগোতে হবে। মানসিক চাপের কারণ অনুসন্ধান করে সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে চাপকে জয় করাই চাপ মোকাবিলা ।
চাপ মোকাবিলার উপায়
সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য চাপ মোকাবিলা করা প্রয়োজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে চাপ মোকাবিলা করার যোগ্যতা থাকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিচে চাপ মোকাবিলা করার কয়েকটি উপায় দেখানো হলো। এ দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই চাপ মোকাবিলা করতে পারব।
১. মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী উপাদান/পরিস্থিতি / ব্যক্তি সনাক্ত করা;
২. শরীর ও মন কীভাবে এ সকল চাপ সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রতি সাড়া দেয়, তা সনাক্ত করা;
৩. চাপ এর জন্য দায়ী উপাদান হ্রাস করা;
৪. নিজেকে শান্ত থাকতে বলা; বার বার বলা। নিজেকে বলতে হবে, কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়;
৫. মনোবল বজায় রাখা;
৬. বন্ধু বা নির্ভরযোগ্য কারো সাথে আলোচনা করা, পরামর্শ করা, শেয়ার করা। সহকর্মী কারো সাথে মনের কষ্টের কথা আলোচনা করলে চাপ লাঘব হয়;
৭. মনে রাখতে হবে, আনন্দ ভাগ করলে বেড়ে যায়, দুঃখ/ কষ্ট/চাপ ভাগ করলে কমে যায়;
৮. গ্রহণযোগ্য পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা;
৯. সময় ব্যবস্থাপনা করা ।
চাপ মোকাবিলার গুরুত্ব
চাপ মোকাবিলার মাধ্যমে একজন মানুষ তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ সাধন হয়। আবেগপ্রবণ মানুষ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। সে তখন কোনো যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয় না। ফলে এ ধরনের মানুষ অনেক সময় নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে । আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাপকে জয় করে এ ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাফল্য অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা আর চাপের কাছে নতি স্বীকার না করা। তোমরা যারা খেলাধুলা কর কিংবা খেলা দেখো- নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ খেলোয়াড়রা নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কীভাবে খেলে যায়। ক্যারিয়ারে বিভিন্ন সময় ঘাত-প্রতিঘাত আসে। অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না কিংবা অনেক চাওয়া অপূর্ণ থেকে যায়। এসব কারণে অনেক সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপ অনুভূত হয়। এ সময় যারা চাপ মোকাবিলা করে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তারা সফলকাম হয় ।সময় ব্যবস্থাপনা
সব ধরনের কাজই কোনো না কোনো নিয়মের মাধ্যমে বা ব্যবস্থাপনার অধীনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এক বা একাধিক ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিতভাবে যেকোনো কাজ সম্পাদন করে। এই পরিকল্পিত তৎপরতাকে ব্যবস্থাপনা বলে। আর সময়ের পরিকল্পিত ব্যবহার হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পিত কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী ভাগ করে এবং বাস্তবায়ন করে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাকে সময় ব্যবস্থাপনা বলে ।
সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়। কাজগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ে ভাগ করে নিলে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করলে সময়মতো কাজ সম্পন্ন হয়। পরিকল্পিত সময়ে পরিকল্পিত কাজ করার ফলে সময়ের অপচয় হয় না। সময় বিভাজন করে সে অনুযায়ী কাজ করলে দেখা যায় কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বাড়তি সময়ে অন্য কাজ করার সুযোগ থাকে। ফলে দেখা যায় অল্প সময়ে অনেক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সময় ব্যবস্থাপনায় যেহেতু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের জন্য সময় বরাদ্দ করা থাকে, তাই কাজের কোনো অংশকেই জটিল মনে হয় না । সময় ব্যবস্থাপনার আর একটি সুবিধা হলো এতে কোনো কাজ জমে থাকে না।সময় ব্যবস্থাপনার মডেল
বিখ্যাত লেখক পিটার ড্রাকার তার “The Effective Executive” গ্রন্থে সময় ব্যবস্থাপনা মডেলের তিনটি ধাপ উল্লেখ করেছেন-
সময় বিশ্লেষণ→ নিরর্ধক চাহিদা চিহ্নিতকরণ কর্ম সম্পাদন
সময় বিশ্লেষণ : প্রত্যেককে তার নিজের কমপক্ষে এক সপ্তাহের সময়ের রেকর্ড রাখতে হবে এবং সময়
বিশ্লেষণ করে কতটুকু সময় প্রকৃতপক্ষে কাজে লেগেছে আর কতটুকু সময় অপচয় হয়েছে তা আলাদা করতে হবে। এক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজনে কাছের কাউকে সাথে রাখা যেতে পারে। নিরর্ধক চাহিদা চিহ্নিতকরণ : সময় বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ করা হয়, যার
কোনো দরকার নেই এবং যা চাইলে বাদ দেওয়া যায়। এ ধরনের কাজগুলো চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং
পরবর্তীতে কাজের মধ্যে যাতে এগুলো ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কর্ম সম্পাদন সময়ানুযায়ী কাজের পরিকল্পনা এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।
পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে কোনো কাজে বিরতি বা ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনো কাজ করা যাবে না। মার্কিন গবেষক Stephen Covey তাঁর সময় ব্যবস্থাপনার চার স্তর বিশিষ্ট মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন- যা 'Covey's Time Managment Quadrant' নামে পরিচিত, নিচে মডেলটি দেখানো হলো:
ক্যারিয়ার গঠনে সময় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা
সময় ব্যবস্থাপনা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। সময়ের যথাযথ ব্যবহার তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনা দেয়। সময়ের প্রতি যারা নিষ্ঠাবান তারা জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ক্যারিয়ারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লক্ষ্যে স্থির থাকা। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে করার অভ্যাসের কারণে একজন শিক্ষার্থী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না । সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার ক্যারিয়ারে কোন কাজের পূর্বে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারে। ফলে সফলতার হার বেড়ে যায়। সময় ব্যবস্থাপনা আমাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার ফলে কাজের ক্ষেত্রে কখনো পিছিয়ে পড়তে হয় না। সময়ের সদ্ব্যবহারের কারণে কাজ করার পর্যায়ে কোনো ভুল হলে তা শোধরানোর সুযোগ থাকে। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহজেই সফল ক্যারিয়ার গঠন করা যায়। মনে রাখতে হবে 'সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না'।প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা
সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ নিজ হাতে সব কাজ করত। ধীরে ধীরে মানুষ চিন্তা করতে লাগল কীভাবে সহজে ও দ্রুত কাজ করা যায় । “প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী" এ প্রবাদকে সার্থক করে মানুষ ধীরে ধীরে এমন সব জিনিস এবং কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে লাগল যা তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমকে অনেকটাই কমিয়ে দিল । মানুষের কাজকে সহজ ও দ্রুত সম্পাদনের জন্য আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কর্মপদ্ধতিকে প্রযুক্তি বলা হয় । কবে, কোথায়, কখন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মানুষ যখন তার কাজকে সহজ করার কোনো পদ্ধতি বা যন্ত্র আবিষ্কার করা শুরু করলো তখন থেকেই প্রযুক্তির জন্ম । আদিম যুগে পশু শিকারের জন্য বল্লম তৈরি করা কিংবা শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন আবিষ্কার করাকে প্রযুক্তির উদ্ভবের প্রাথমিক অবস্থা বলে স্বীকার করা হয়। তবে প্রযুক্তিবিদেরা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সময় থেকেই মূলত প্রযুক্তির উদ্ভব। এককথায়, প্রযুক্তি হলো কিছু প্রায়োগিক কৌশল, যা মানুষ তার পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করে ।
প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব
অনেক কাজ আছে যা সাধারণভাবে করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোনো কাজ খুব সহজেই করা যায়। যেমন আগে ধান মাড়াই করতে অনেক সময়ের দরকার হতো আর এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অনেক ধান মাড়াই করা যায়। এতে মানুষের সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। যেমন পূর্বে পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় করা ছিল অনেক কঠিন কাজ আর এখন মুহূর্তেই কম্পিউটার দিয়ে ফলাফল তৈরি করা যায়। এখন প্রযুক্তির সহায়তায় প্রায় নির্ভুল কাজ করা সম্ভব। কম্পিউটারের সাহায্যে হাজার হাজার তথ্য থেকে গবেষণা করে নির্ভুল প্রতিবেদন তৈরি সম্ভব। প্রযুক্তির সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো কাজের ফলাফল জানা যায়। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এখন পরীক্ষার দিনই প্রকাশিত হচ্ছে। এটি প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি বড় দৃষ্টান্ত ।
প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন
প্রযুক্তি কী, প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে করতে হয়, কোথায় কোথায় প্রযুক্তির ব্যবহার করা সম্ভব, কোন যন্ত্রের কী কাজ, যন্ত্রগুলো কীভাবে কাজ করে এসব বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে। বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে অনেকের মধ্যে ভীতি কাজ করে। প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এই ভয় কাটিয়ে উঠে আগ্রহ নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু না করলে তা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। যে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ মানুষকে দক্ষ করে তোলে। তাই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির ব্যবহারে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ।
ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ব্যবহার
বর্তমানে ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যতম একটি দক্ষতা। দিন দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যতই ঘটছে সবকিছু ততই প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থালীর কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ কাজই এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফরম তোলা ও জমা দেয়া, টাকা জমা দেয়া, পরীক্ষার ফলাফল জানা ইত্যাদি কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা থাকলে শিক্ষার্থীরা অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই কাজগুলো সম্পাদন করতে পারবে। এছাড়াওকর্মক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে । চাকরির আবেদন করা, পরীক্ষা দেওয়া, বাস, ট্রেন, বিমানের টিকেট ক্রয় ইত্যাদি প্রযুক্তির সাহায্যেই হচ্ছে। তাই ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করার বিকল্প নেই।
গাণিতিক দক্ষতা
মানুষের জীবনের সাথে জড়িত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ অন্যতম । জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি স্তরে, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে মানুষকে নানারকম হিসাব করতে হয় । সভ্যতার শুরু থেকেই হিসাব-নিকাশের এ ধারা চলে আসছে। মানুষের হিসাব-নিকাশের এ ধারাকে বইয়ের ভাষায় বলা হয় গাণিতিক দক্ষতা। গাণিতিক দক্ষতা বা গাণিতিক জ্ঞান হচ্ছে গণিতের সাধারণ ধারণাকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগানো। গাণিতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সহজেই তার প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক জীবনের হিসাব-নিকাশের প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে। গণনা করতে পারা, যোগ বিয়োগ, হিসাব রাখা, পরিমাণ ও পরিমাপ বোঝা, ভূমি বা জমির হিসাব বোঝা, পরিসংখ্যান বোঝা ইত্যাদি হচ্ছে গাণিতিক দক্ষতার উদাহরণ । গাণিতিক দক্ষতার তিনটি স্তর রয়েছে; যেমন:
১. সংখ্যা পরিচয় ও সাধারণ যোগ-বিয়োগ, সাধারণ হিসাব-নিকাশ (প্রাথমিক ধারণা)
২. প্রয়োজনীয় জীবনঘনিষ্ঠ গাণিতিক দক্ষতা
৩. উচ্চতর গাণিতিক দক্ষতা
গাণিতিক দক্ষতার গুরুত্ব
মানব জীবনে গাণিতিক দক্ষতার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মানুষ নিজের অজান্তেই গাণিতিক দক্ষতার সাহায্যে
সকল কাজ করে থাকে। যেমন: সংসারের বাজেট, ব্যবসায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ করা। গাণিতিক দক্ষতা মানুষকে যৌক্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; এর মাধ্যমে মানুষ সবকিছু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শেখে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও গাণিতিক দক্ষতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । যেমন একজন কৃষক জমিতে ফসল বোনা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত যাবতীয় কাজের মূল্য নির্ধারণ করেন। তার বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি তিনি বুঝতে পারেন। ফলে পরবর্তী সময়ে তার পক্ষে চাষাবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। এমনিভাবে মানুষের জীবনে গণিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের উপায়
গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গণিতের প্রাথমিক বিষয়গুলো আয়ত্তে নেয়া। এরপর জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ গাণিতিক পন্থায় সম্পন্ন করলে গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন কঠিন ও জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ, নিজের ঘরের পরিমাপ, জমির মাপ-ঝোখ ইত্যাদি নিজেই করার চেষ্টা করতে হবে। গাণিতিক দক্ষতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া গণিতের উপর বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে গাণিতিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায় ।ক্যারিয়ার গঠনে গাণিতিক দক্ষতার ব্যবহার
একজন শিক্ষার্থী জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। এসব চড়াই-উত্রাই পার হওয়ার জন্য নানান হিসাব-নিকাশ, যোগ-বিয়োগ করে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে হয়। এসব করার জন্য গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করা হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে গাণিতিক দক্ষতার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কখনো কোনো একটি কাজ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়; যারা গাণিতিকভাবে দক্ষ তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে কত গতিতে কাজ করলে যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় বা নিয়োগ পরীক্ষায় গাণিতিক দক্ষতা নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করা হয়; এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক । কর্মক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় পরিসংখ্যানভিত্তিক কিছু কাজ এসে পড়ে, যা গাণিতিক দক্ষতা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয় । এজন্য ক্যারিয়ারকে সুগঠিত করার জন্য গাণিতিক দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি
বাংলা নান্দনিক শব্দটি নন্দন থেকে এসেছে। নন্দন শব্দের অর্থ হলো যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যার দ্বারা আনন্দ লাভ করা যায়। যেহেতু আনন্দের উৎস হচ্ছে সৌন্দর্য তাই নন্দন শব্দের অর্থকে সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করা যায় । আর নান্দনিক- এর অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্যমণ্ডিত। যেকোনো কাজ সুন্দর করে গুছিয়ে করা যা দেখলেই সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয় তাকে নান্দনিকতা বলে। এই নান্দনিকতা যেমন হতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি হতে পারে কবিতার ক্ষেত্রে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ কাজেও নান্দনিকতা বিদ্যমান ।
কোনো কাজের ক্ষেত্রে কাজটিকে সুন্দর করে করার, সুন্দরভাবে কাজ করানোর বা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার যে বোধ, মনোভাব বা মানসিকতা তাকে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে ।
নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব
সবাই সুন্দরের পূজারি। কোনো কিছুর সৌন্দর্য বিচার করতে কিংবা সৌন্দর্য থেকে আনন্দ অনুভব করতে গেলে নান্দনিকতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে নান্দনিক। যার দৃষ্টিভঙ্গি নান্দনিক নয় তার পক্ষে সুন্দরকে সুন্দর হিসেবে বিচার করাই সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গি নান্দনিক হলে মানসিক তৃপ্তি লাভ করা যায়, আনন্দের সাথে কাজ করা সম্ভব হয় ।
ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা
গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন শিক্ষার্থী যদি তার ওপর অর্পিত কাজগুলো গুছিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে তবে শিক্ষক, সহপাঠী ও অন্যরা তার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তাকে সহযোগিতা
সুন্দরভাবে কাজ করার গুরুত্ব অন্যরকম। কারণ সুন্দর কাজকে সবাই পছন্দ করে। কোনো পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতায় যদি হাতের লেখা গোছানো হয় ও উপস্থাপনা সুন্দর হয় তবে শিক্ষক তাকে একটু আলাদা করে বিবেচনা করেন। ঐ শিক্ষার্থী শুধু সৌন্দর্যের কারণে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি নম্বর পায় । ক্যারিয়ার করতে প্রস্তুত থাকে। একইভাবে কর্মক্ষেত্রেও সে যদি তার কাজে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় তবে সে অন্যদের তুলনায় আলাদাভাবে বিবেচিত হয় এবং তার সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচুতে উঠে যায় । সবাই তার নৈকট্য লাভ করতে চায় ও তাকে ভালোবাসে ।
Promotion